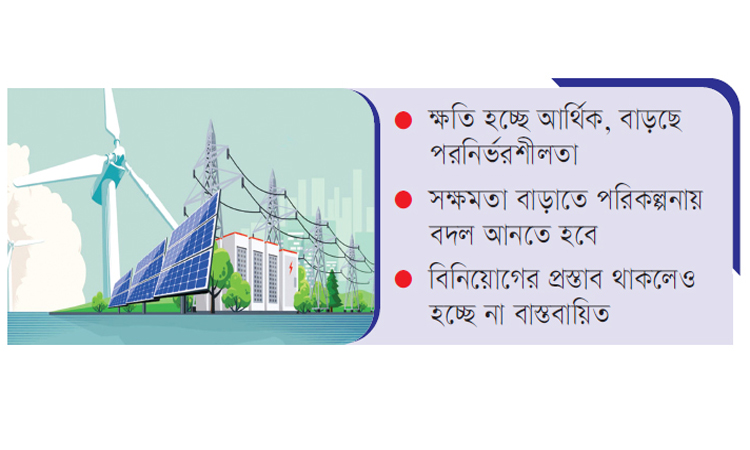
বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেই নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। তবে ব্যবহারের বড় অংশই দখলে রেখেছে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো। তাপমাত্রার তীব্রতায় বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সরাসরি প্রভাব দেখছে বাংলাদেশ। এমন বাস্তবতায় জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে ফিরতে জনমত বাড়ছে। তবে প্রযুক্তি ও উপকরণের উচ্চমূল্যে ব্যাহত হচ্ছে গ্রীন এনার্জি উৎপাদন। আর এসব কারণে নীতিমালা তৈরী করলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে পিছিয়ে বাংলাদেশ।
কার্বন গ্যাসের শক্তিশালী স্তর সূর্যের তাপ ফিরতে দিচ্ছে না বায়ুমণ্ডলে। আবার এ ধরনের গ্যাস উৎপাদনের উৎসও কমছে না। দেশে জলবিদ্যুৎ, সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার পুরোনো, পারমাণবিক বিদ্যুতেও এগিয়েছে দেশ। কাপ্তাইয়ের পর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আর আসেনি। সৌর বিদ্যুতেও অতটা সফলতা দেখা যায়নি। পুরোনো প্রযুক্তি, দাম বেশী ও সোলার প্যানেলে জায়গাও বেশী প্রয়োজন হয়।
দেরীতে হলেও দেশের স্থলভাগে এখন কমপক্ষে দশটি বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চলমান। কিন্তু সমুদ্র বুকে সম্ভাবনা সত্ত্বেও তেমন চেষ্টা নেই। নদী প্রধান দেশ হলেও তীরে বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র নেই। বলা হচ্ছে, কম চাপে বাণিজ্যিক উৎপাদন লাভজনক হবে না নদীর তীরে। সে কারণে প্রযুক্তিও সহজলভ্য নয়।
কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট ম্যানেজার প্রকৌশলী মুকিত আলম খান বলেন, ‘আমাদের এ কোস্টাল এরিয়া ছাড়া যদি আমরা বাংলাদেশের ভেতরের দিকে যাই সেই এনার্জি প্রডাক্টশনটা অনেক ক্ষেত্রেই ড্রপট করবে। সেটা আসলে বাণিজ্যিকভাবে সফল হবে না।’
প্রকৌশলী মুকিত আলম খান বলেন, ‘এ মুহূর্তে টেকনোলজি কিনে আনা ছাড়া কোনো সেকেন্ড সোর্স নেই। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামালের দরকার হয়, যেগুলোর জোগান বাংলাদেশে নেই।’
জ্বালানী বিশেষজ্ঞ ও কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যাবের জ্বালানী উপদেষ্টা অধ্যাপক সামসুল আলম বলেন, ‘আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানীর বাজার তৈরী হয়নি। এ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি নিম্নমানের। নবায়নযোগ্য জ্বালানী নিয়ে কোনো বিনিয়োগও নেই, কোনো পরিকল্পনাও নেই। বিশ্বেও অন্যান্য দেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে এগিয়ে গেছে কারণ তাদের নীতি-পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের দেশের মতো দুর্নীতি নেই।’
‘আমরা গ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদনে আছি। ফলে ফসিল ফুয়েল আমদানীর বাজার প্রমোট করছি, আনইকোনোমিক ওয়েতে গ্রিড সম্প্রসারণ করছি। এ ছাড়া আমরা এখন বিদ্যুতে শতভাগ সাবসিডি দিচ্ছি আবার জ্বালানিতেও দিচ্ছি। এটাই হচ্ছে পলিসি।’ অধ্যাপক সামসুল আলম মনে করেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে যাওয়ার জন্য সরকারের পলিসি বদলানোর কোনো বিকল্প নেই। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তেল-গ্যাস-কয়লার বিকল্প হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর দিকে ঝুঁকছে বিশ্ব। ইতোমধ্যে অনেক উন্নত দেশ ব্যবহূত জ্বালানীর ৩০ শতাংশ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য উৎস থেকে জোগান দিচ্ছে। সে তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো। বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার জোর দেয়া হলেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) তথ্য অনুযায়ী, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্জন করা গেছে তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম। ফলে আর্থিক ক্ষতি যেমন হচ্ছে, বাড়ছে পরনির্ভরশীলতা। দেশে শুধু সৌরশক্তি থেকেই উৎপাদন হচ্ছে ৬৭৫ দশমিক ২ শতাংশ বা মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ৭৪ শতাংশ। এছাড়া বায়ু থেকে আসছে ২ দশমিক ৯ শতাংশ, হাইড্রো থেকে ২৩০ মেগাওয়াট, বায়োগ্যাস থেকে দশমিক ৬৯ শতাংশ ও বায়োম্যাস থেকে দশমিক ৪ শতাংশ। সেক্ষেত্রে খাতটির অর্জন আসলে আরো কম। অথচ সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে চলতি বছরের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ পৌঁছানোর কথা ছিল আড়াই হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় বদল আনতে হবে। শুধু প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিপণ্য কিনতে ভিনদেশের দিকে না তাকিয়ে এদেশের উপযোগী করে উপকরণ তৈরীতে আরো গবেষণা বাড়ানো প্রয়োজন বলেই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।
কয়লা, তেল, এলএনজির মতো জীবাশ্ম জ্বালানীগুলোই মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনে সবচেয়ে বড় উৎস। এ উৎসগুলো গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী। যার কারণে আমরা অব্যাহতভাবে তাপপ্রবাহ-দাবদাহের মতো ঘটনা দেখি। কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ উৎপাদনও থামিয়ে রাখা যাবে না সেই বাস্তবতায় সারা বিশ্বের দেশগুলো নবায়নযোগ্য জ্বালানীর দিকে ঝুঁকছে। তারা স্বৈরবিদ্যুৎ এবং বায়ুচালিত বিদ্যুতের দিকে যাচ্ছে তখন আমরা কেন পিছিয়ে থাকব। কক্সবাজারের এ বায়ুকল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেই আশার আলোই দেখাচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌর, বায়ু ও পানির মতো উৎসকে কাজে লাগিয়ে চাহিদামাফিক বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও বিশ্বের উন্নত দেশগুলো নবায়নযোগ্য শক্তিকে কাজে লাগিয়েই জ্বালানী খাতকে এগিয়ে নিচ্ছে। এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে, এক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যও পেয়েছে দেশটি। ২০১৮ সালে নবায়নযোগ্য বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনসংক্রান্ত একটি বছরভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয়। ওই পরিকল্পনায় ২০১৮ সালকে ভিত্তি বছর ধরে পরবর্তী তিন বছরের (২০২১ পর্যন্ত) সম্ভাব্য অর্জনের একটি হিসাব করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী নানা ধরনের প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছিল। এ অনুযায়ী, ২০১৮ সালে নবায়নযোগ্য বিভিন্ন উৎস থেকে মোট ৫৮৪ দশমিক ৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ার কথা ছিল। এরপর ২০১৯ সালে নতুন ৪৩২ দশমিক ৫ মেগাওয়াট, ২০২০ সালে ৬০৪ দশমিক ৫ ও ২০২১ সালে ৫৫৫ দশমিক ৫ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।
নবায়নযোগ্য জ্বালানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলে স্রেডার সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে প্রথমত অনভিজ্ঞতা, তারপর এটিকে ব্যবহারোপযোগী করতে কর্মপরিকল্পনায় দেরী হওয়া এবং এ জ্বালানীর জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন সেটির সংকট— এই সবকিছু মিলিয়েই নবায়নযোগ্য জ্বালানীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। তবে এখন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে তিনি বলেন, সোলার সিস্টেম নিয়ে আমরা এগোনোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেটার ক্যাপাসিটি খুবই কম। পাঁচ লাখ সোলার সিস্টেম থেকে মাত্র ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তা ছাড়া সোলার নিয়ে বড় আকারে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমরা জায়গা সংকটে পড়েছি। এত বড় প্রকল্প করতে গেলে ৩৫০ একর জমির প্রয়োজন ছিল। যেটি আমরা করতে পারিনি। এছাড়া টেকনোলজি ডেভেলপ করাটাও বড় একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। স্রেডার তথ্য অনুযায়ী, নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ পর্যন্ত মোট ৪০টির অধিক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, যার বেশীর ভাগই গৃহীত হয়েছে ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেশের ২৫ জেলায় স্থাপিত সোলার পার্ক থেকে মোট ২ হাজার ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় ৭ দশমিক ৪ মেগাওয়াট, পঞ্চগড় সদর উপজেলায় আট, কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় ২০ ও জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার তিন মেগাওয়াট সক্ষমতার চারটি সোলার পার্কের কাজ শেষ হয়েছে। এর বাইরে ময়মনসিংহে নির্মিত এখন পর্যন্ত দেশের বৃহত্তম সোলার পার্কও এরই মধ্যে উৎপাদনে চলে এসেছে।
নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার কারণ জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইফুল হক বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে পিছিয়ে থাকার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে বেশ সময় লেগেছে। ৩০ বছর আগে থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানী নিয়ে কাজ শুরু হলেও বাংলাদেশ এটি ২০০৮-১০ সালের দিকে শুরু হয়েছে। গত ১৪ বছরে নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে ভালো ধারণা ও দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে সময় লেগে গেছে।
তিনি বলেন, দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ বিভাগ ছিল জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর। ফলে অন্যান্য উৎসকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এখনো বেশ কঠিন। তাছাড়া এ প্রযুক্তি থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতো, সেগুলো ছিল উচ্চমূল্যের। এখন দাম কমে এসেছে, ফলে এখন বিনিয়োগ হচ্ছে।
নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার বিষয়ে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, প্রতিবন্ধকতা হলো আমাদের পর্যাপ্ত জমি নেই, সোলার ছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনের তেমন কোনো উপায় নেই। তবে তিনি জানিয়েছেন, এখন ৩ পার্সেন্ট নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদন করলেও ২০৫০ সাল নাগাদ ৫০ পারসেন্ট উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন তারা।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডির তথ্য মতে, নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতে বিদেশী বিনিয়োগের অনেক প্রস্তাব থাকলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাদের হিসাবে ৩৬টি প্রকল্পের মধ্যে আটটি বাস্তবায়ন হয়েছে। বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইপিপিএ) সভাপতি ইমরান করিম বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর বিষয়ে প্রথমত আমাদেরকে খরচের দিকে নজর দিতে হবে। সৌরবিদ্যুৎ করার জন্য অনেক জায়গা লাগে। আমাদেরকে নেপাল থেকে পানিবিদ্যুৎ আমদানির জন্য এখনই পরিকল্পনা নিতে হবে। এ ছাড়া এমন অনেক প্রযুক্তি আসছে যেগুলো এখন একটু কস্টলি হলেও ভবিষ্যতে তা থাকবে না। সেদিকে সরকারের নজর দিতে হবে। এক হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে ব্যবহূত মোট জ্বালানির ৯০ শতাংশ আমদানী করে ব্যবহার করতে হবে। তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানীতে সক্ষমতা বাড়ালে সবদিক থেকে লাভবান হবে বাংলাদেশ। ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ। দেশটি ‘ফার্স্ট প্রজেক্ট’ চালু করেছে কপ২৮-কে সামনে রেখে। দেশটি প্রত্যাশিত সীমার আগেই কয়লা বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে চায়। ইন্দোনেশিয়ার নবায়নযোগ্য জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ইয়ুদো প্রিয়াদি বলন, ‘বিষয়টি এখনো আলোচনার পর্যায়ে। কয়লার ব্যবহার আরো আগেই কমিয়ে ফেলা হবে। কয়লা শিল্পের অর্থায়নে প্রধান ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের বিবেচনাই পরিবেশ অনুকূল জ্বালানী গ্রহণ করতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে। ইন্দোনেশিয়া ২০৬০ সালের মধ্যে কার্বন নিরপেক্ষ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। কয়লা ব্যবহার থেকে সরে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশে মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশী মানুষ খাতটিতে কাজ করছে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার এ পদক্ষেপে প্রভাব পড়বে সামাজিকভাবেই।
পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান রিস্টাড এনার্জি জানিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ব্রিকস ৮০ শতাংশের বেশী জ্বালানী নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও অনুকূল পরিবেশ দিতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্পদ ও সাশ্রয়ী শ্রম সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারে বৈশ্বিক জ্বালানী সংকট মোকাবিলায়।
নয়া শতাব্দী/এসআর
মন্তব্য করুন
আমার এলাকার সংবাদ